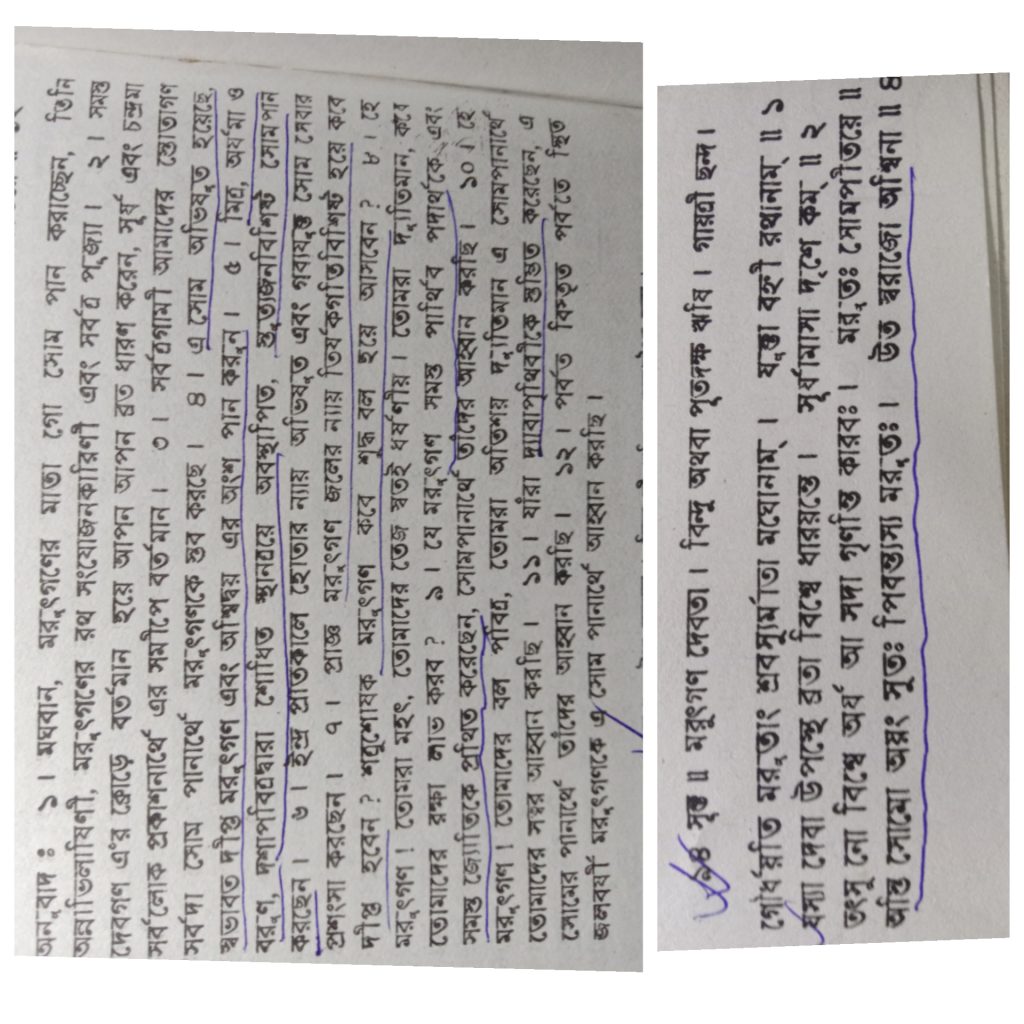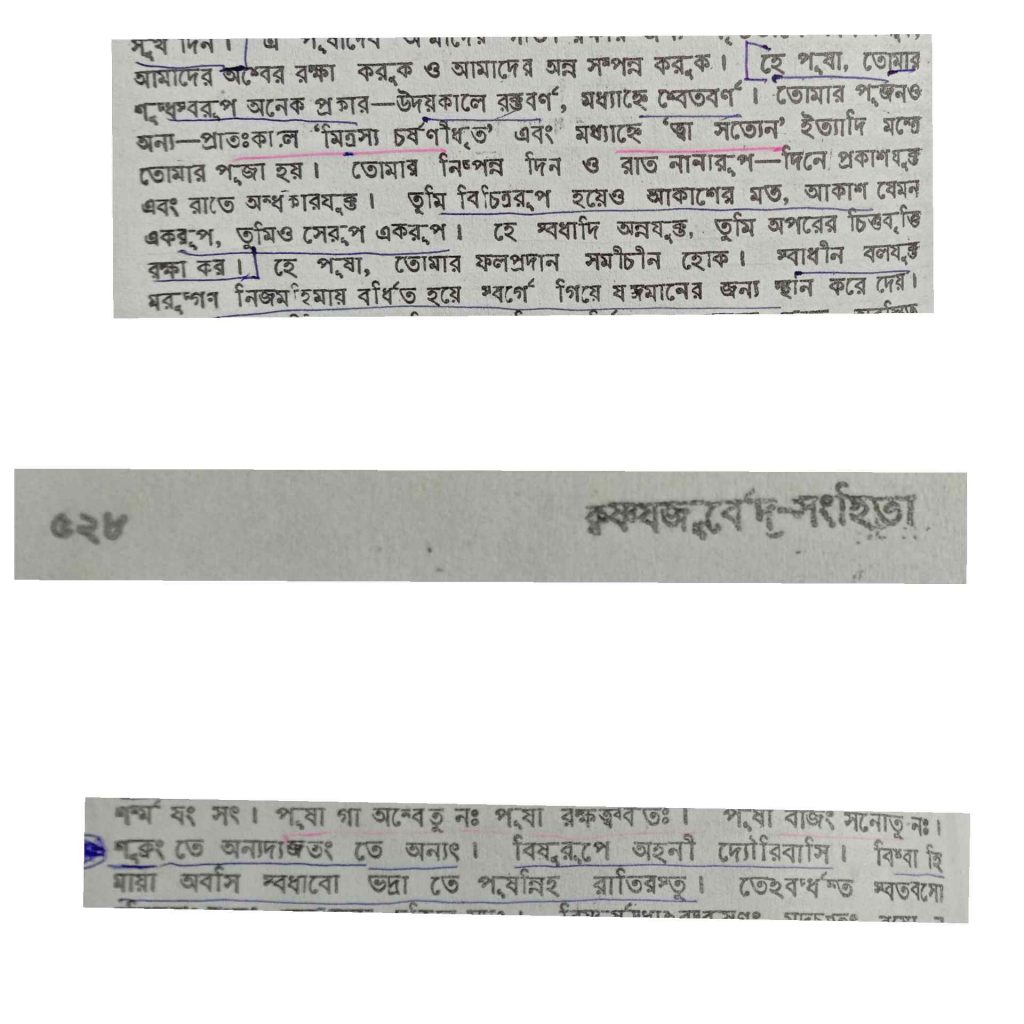Line 1.
‘Gou’ means cows or rays. Here ‘rays’ will be appropriate. ‘Marut’ is hot air and vapours.That is mostly formed from ocean for Sun Rays. Marut is the source of cloud and rain.
Mogho means great. This work of the Maruts is really Great.
Shraba is Creating.
Look here the Hymn/ Sukta.
“Gou r Dhayati Marutam, Shraba syu r Mata Maghonam.”
Rays are the creator and the mother of the Great Marutas.
Reek Veda, 8th Mandolom.